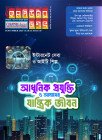হোম > ই-পাসপোর্ট : চোখের পলকে খুলবে বন্দরের ফটক
লেখক পরিচিতি
লেখকের নাম:
ইমদাদুল হক
মোট লেখা:৬২
লেখা সম্পর্কিত
পাবলিশ:
২০১৮ - জুন
তথ্যসূত্র:
কমপিউটার জগৎ
লেখার ধরণ:
ই-পার্লামেন্ট
তথ্যসূত্র:
ই-প্রযুক্তি
ভাষা:
বাংলা
স্বত্ত্ব:
কমপিউটার জগৎ
ই-পাসপোর্ট : চোখের পলকে খুলবে বন্দরের ফটক
আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগেই ই-পাসপোর্ট যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে এই প্রযুক্তিটি চালু হয়ে গেছে বিশ্বের ১১৯টি দেশে। এসব দেশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, বুুলগেরিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স. জার্মানি, গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, আরব আমিরাত, ইরান, ইরাক, জাপান, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ভারতে এই সেবা চালু হয়েছে। এবার এই কাতারে নাম লেখাচ্ছে বাংলাদেশ।এর ফলে পাসপোর্টপ্রতি সরকারের সাশ্রয় হবে প্রায় ৩ ডলার। অন্যদিকে দায়িত্বরত কর্মকর্তার হাতে কাগুজে বা মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট দিয়ে অনুমতির জন্য ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না ব্যবহারকারীকে। ইলেকট্রিক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ই-পাসপোর্ট ধরতে চোখের পলকেই খুলে যাবে বহিরাগমনের পথ।
গেট পাস থেকে ই-পাসপোর্ট
কোনো একটি দেশের নির্দিষ্ট ভূখন্ড থেকে অপর একটি দেশের বন্দরে যাওয়ার অনুমতি হচ্ছে পাসপোর্ট (পাস + পোর্ট)। এর প্রচলন শুরু হয় মধ্যযুগে।ব্রিটেনের রাজা পঞ্চম হেনরির সময়ে। ওই সময়ে শুরুতে ইউরোপের দেশগুলোর কোনো শহর বা নগরে প্রবেশ করতে চাইলে নগর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গেটপাস নিতে হতো বিদেশি পর্যটক বা পরিব্রাজকদের। ১৫৪০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গেটপাস আইন ১৪১৪ হয় এবং ট্রাভেল ডকুমেন্ট হিসেবে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। এরপর ১৭৯৪ সালে তারা সরকারি চাকুরেদের জন্য পাসপোর্ট ইস্যু করে।
বিশ্বকোষ অনুযায়ী, আনুমানিক ৪৫০ খ্রিস্টাব্দে হিব্রু বাইবেলের নেহেমিয়া ২ঃ৭-৯তে পাসপোর্টের অনুরূপ কাগজের নথির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর মধ্যযুগীয় ইসলামিক খেলাফতের সময়, শুল্ক প্রদানের রসিদ ছিল এক ধরনের পাসপোর্ট। যারা জাকাত (মুসলিমদের জন্য) ও জিজিয়া কর (জিম্মিদের জন্য) প্রদান করত, শুধু সেইসব মানুষ খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতে পারত। এভাবে শুল্ক প্রদানের রসিদ ভ্রমণকারীদের জন্য পাসপোর্টের অনুরূপ ছিল।
তবে আন্তর্জাতিকভাবে আধুনিক পাসপোর্টের ধারণা শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে। মূলত, দেশগুলো নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এর ওপর জোর দেয়। তখন প্যারিসে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (লিগ অব ন্যাশনস) বৈঠকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কাগজের তৈরি পাসপোর্ট এবং আনুষঙ্গিক অন্য নিয়মকানুন চালু করা হয়। ১৯৮০ সালের পর আসে এমআরপির ধারণা। বাংলাদেশে এর প্রচলন শুরু হয় ২০১০ সালে। অবশ্য এর দু’বছর আগেই ২০০৮ সাল থেকে কন্টাক্টলেস স্মার্টকার্ড প্রযুক্তির (বায়োমেট্রিক পদ্ধতিনির্ভর) ডিজিটাল পাসপোর্ট বা ই-পাসপোর্ট চালু হয়। ওই বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের ৬০টি দেশ এই পাসপোর্ট চালু করে। নিরাপত্তা চিহ্ন হিসেবে ই-পাসপোর্টে থাকে চোখের মণির ছবি ও আঙুলের ছাপ। আর এর পাতায় থাকা চিপসে সংরক্ষিত থাকে পাসপোর্টধারীর সব তথ্য।
ই-পাসপোর্ট যুগে বাংলাদেশ
২০১৬ সালের ২৪ এপ্রিল পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ উদ্বোধনের সময় ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই অংশ হিসেবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০) আধুনিক ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ই-পাসপোর্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এরপর শেখ হাসিনার জার্মানি সফরের সময় ২০১৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে জার্মানির সরকারি প্রতিষ্ঠান ভেরিডোস জেএমবিএইচের সাথে সমঝোতা স্মারক সই হয়।
সরকারের বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিফতর সূত্র মতে, গত ১৫ মে অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ই-পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী ৫ জুন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে ই-পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব। প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে সরকারিভাবে বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা দেবে জার্মানি।
গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত কারিগরি কমিটির মোট ছয়টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এসব সভার তিনটিতে বাংলাদেশে জার্মানির রাষ্ট্র্রদূত ও উপরাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনা বিভাগ থেকে ই-পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব দ্রুত একনেক সভায় উত্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে তাগিদ দেয়া হয়।
এদিকে ই-পাসপোর্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জার্মানির একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে জুন-জুলাইয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি জানিয়েছেন, সরকার আশা করছে ডিসেম্ব^রের মধ্যে ই-পাসপোর্ট চালু করা সম্ভব হবে। তবে সেটা পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যাবে জার্মানির প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি হওয়ার পর। কারণ, কাজটা তারাই করবে। তারা যদি বলে ডিসেম্ব^রের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে না, সে ক্ষেত্রে সময় এক-দুই মাস বেশি লেগে যেতে পারে।
এমআরপি থেকে ই-পাসপোর্ট
মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বা এমআরপি হচ্ছে এমন একটি পাসপোর্ট, যাতে আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্য জলছাপের মাধ্যমে ছবির নিচে লুকায়িত থাকে। একই সাথে এতে থাকে একটি ‘মেশিন রিডেবল জোন (গজত)’, যা পাসপোর্ট বহনকারীর ব্যক্তিগত তথ্যবিবরণী ধারণ করে। এমআরজেড লাইনে লুকায়িত তথ্য শুধু নির্দিষ্ট মেশিনের মাধ্যমে পড়া যায়।
অন্যদিকে ই-পাসপোর্ট নামে পরিচিত বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের মতোই। তবে এতে স্মার্টকার্ড প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এই কার্ডে একটি মাইক্রোপ্রসেসর চিপ এবং অ্যান্টেনা বসানো থাকে। এ পাসপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাসপোর্টের ডাটা পেজ এবং চিপে সংরক্ষিত থাকে। ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও) ডক ৯৩০৩-এ এই ডকুমেন্ট ও চিপ সংক্রান্ত তথ্য জমা রাখা হয়। তবে বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু আছে এমন দেশগুলো এ সংস্থার পাবলিক কি ডিরেক্টরির (পিকেডি) অংশ।
সুবিধা-অসুবিধার ই-পাসপোর্ট
ই-পাসপোর্টের আইডেন্টিফিকেশন ব্যবস্থায় বর্তমানে ফেসিয়াল, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং আইরিস রিকগনিশন বায়োমেট্রিকস ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে আইসিএও পাসপোর্টে ব্যবহার্য বায়োমেট্রিক ফাইল ফরম্যাট এবং যোগাযোগ প্রটোকল নির্ধারণ করে দেয়। ডিজিটাল ছবি চিপে শুধু ডিজিটাল ছবিই সংরক্ষিত রাখা হয়, যা সাধারণত জেপিইজি বা জেপিইজি২০০০ ফরম্যাটের হয়ে থাকে। পাসপোর্ট চিপের বাইরে ইলেকট্রনিক বর্ডার কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে এই বায়োমেট্রিক ফিচারগুলোর মধ্যে তুলনা করা হয়।
কন্টাক্টবিহীন চিপে ডাটা সুরক্ষিত রাখতে এতে কমপক্ষে ৩২ কিলোবাইট ‘ইইপিআরওএম, সংক্ষেপে ইইপিরম (ঊঊচজঙগ)’ স্টোরেজ মেমরি থাকে এবং তা আইএসও/আইআইইসি ১৪৪৪৩ আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডসহ আরও কিছু স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী একটি ইন্টারফেসে পরিচালিত হয়। তবে বিভিন্ন দেশ এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানভেদে এই স্ট্যান্ডার্ড ভিন্ন হয়ে থাকে। ইইপিরমের মানে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালি ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিড-অনলি মেমরি। এটি একটি বিশেষ ধরনের মেমরি, যা কমপিউটার এবং ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলোয় ব্যবহার করা হয়। এতে অপেক্ষাকৃত কম জায়গা থাকলেও এর প্রতিটি বাইট আলাদাভাবে মুছে ফেলা বা আবার প্রোগ্রাম করা যায়। এর ফলে পাসপোর্টের তথ্য আপডেট করতে কোনো সমস্যা হবে না।
ই-পাসপোর্টে ঝুঁকি
বায়োমেট্রিক পাসপোর্টে সাইবার আক্রমণ ঠেকাতে নন-ট্রেইসেবল চিপ ব্যবহারসহ আরও কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু থাকে। বিভিন্ন চিপ আইডেন্টিফায়ার প্রতিটি আবেদনের বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন চিপ নাম্বার দিয়ে থাকে। পাসপোর্ট চিপে রক্ষিত তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পিকেআই) ব্যবহার হয়, যার ফলে সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে চালু অবস্থায় এ ধরনের পাসপোর্ট নকল করা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়বহুল। একইসাথে ই-পাসপোর্টের ডাটা প্রাইভেসি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শুরু থেকেই। অনেক দেশেই এ নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অভিযোগ হচ্ছে, পাসপোর্টের ডাটা তারবিহীন আরএফআইডি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্রান্সফার করা যেতে পারে, আর এ কারণে ঘটতে পারে বড় ধরনের ডাটা হাতিয়ে নেয়ার ঘটনা। যদি পাসপোর্টের চিপে থাকা ব্যক্তিগত তথ্য আর পাসপোর্ট নাম্ব^ার সঠিকভাবে এনক্রিপ্ট করে না রাখা হয়, তাহলে এই তথ্য যেকোনো সময় অপরাধীদের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
ই-পাসপোর্টের ডাটা সুরক্ষা পদ্ধতি
সাধারণত বেসিক, প্যাসিভ, অ্যাকটিভ ও এক্সটেন্ডেড পদ্ধতিতে ই-পাসপোর্টের ডাটা সুরক্ষা করা হয়। আর তথ্য যাচাই করতে অটোমেটিক বর্ডার কন্ট্রোল সিস্টেমে (ই-গেট) ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষার বর্ণ নিয়ে গঠিত নামগুলোর ক্ষেত্রে পাসপোর্টের নন-রিডেবল জোনে লোকাল স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে উচ্চারণের জটিলতা দূর করে। তবে মেশিন-রিডেবল জোনের ক্ষেত্রে আইসিএওর স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ভিন্ন উচ্চারণভঙ্গির বর্ণগুলোকে সরল রূপ দেয়া হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি ম্যাপিং অনুসরণ করা হয়।
ক. বেসিক অ্যাকসেস কন্ট্রোল (বিএসি) পদ্ধতিতে চিপ এবং রিডারের মধ্যে যোগাযোগ সুরক্ষিত রাখতে এনক্রিপটেড তথ্য বিনিময় করা হয়। চিপের তথ্য পড়ার ক্ষেত্রে মেশিন রিডেবল জোন থেকে প্রাপ্ত একটি ‘কি’প্রবেশ করাতে হয়। মেশিন রিডেবল জোনে ব্যবহারকারীর জন্ম তারিখ, পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ এবং ডকুমেন্ট নাম্বার অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিএসি ব্যবহারের কারণে আক্রমণকারীরা যথাযথ ‘কি’ না জেনে তথ্যে আড়ি পাততে পারে না। তবে বিএসির কিছু দুর্বলতার কারণে বর্তমানে এর বিকল্প হিসেবে সাপ্লিমেন্টাল অ্যাক্সেস কন্ট্রোল (এসএসি) চালু রয়েছে।
খ. প্যাসিভ অথেনটিকেশন (পিএ) পদ্ধতিতে পাসপোর্ট চিপে রক্ষিত তথ্যে কোনো পরিবর্তন চিহ্নিত করতে ব্যবহার হয়। চিপে একটি এসওডি ফাইল থাকে, যাতে চিপে রক্ষিত সব তথ্যের হ্যাশ ভ্যালু এবং এদের একটি ডিজিটাল সিগনেচার উল্লিখিত থাকে। চিপের কোনো তথ্য পরিবর্তন করা হলেই হ্যাশ ভ্যালুর ভিন্নতা থেকে তা শনাক্ত করা হয়। বায়োমেট্রিক পাসপোর্টে পিএ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। এখানে একটি ডিজিটাল স্বাক্ষর রাখা হয়, এটি রাষ্ট্রের সাইনিং কি সংবলিত একটি ডকুমেন্ট সাইনিং কি ব্যবহার করে বানানো হয়।
গ. অ্যাকটিভ অথেনটিকেশন (এএ) পদ্ধতিতে ব্যবহার করে নকল পাসপোর্ট চিপ তৈরি ঠেকানো হয়। এতে একটি ব্যক্তিগত ‘কি’ থাকে, যা নকল করা সম্ভব না হলেও এর অস্তিত্ব সহজেই প্রমাণ করা যায়।
ঘ. এক্সটেন্ডেড অ্যাকসেস কন্ট্রোল (ইএসি)পদ্ধতিতে ব্যবহারে চিপ এবং রিডার উভয়েরই নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করা হয়। এই ব্যবস্থা সাধারণত ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং আইরিস স্ক্যান সুরক্ষিত রাখতে ব্যবহার হয় এবং এর এনক্রিপশন সিস্টেম বিএসির তুলনায় শক্তিশালী। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে সব রকম ডকুমেন্টের জন্যই ইএসি ব্যবহার বর্তমানে বাধ্যতামূলক।
এ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও কিছু দেশে চিপে অনধিকার প্রবেশ ঠেকাতে পাসপোর্ট কাভারের নিচে খুবই পাতলা ধাতব পাত ব্যবহার করা হয়।
আমাদের ই-পাসপোর্ট
বর্তমানে বই আকারে যে পাসপোর্ট আছে, ই-পাসপোর্টের একই ধরনের বই থাকবে। তবে বর্তমানে পাসপোর্টের বইয়ের শুরুতে ব্যক্তির তথ্য সংবলিত যে দুটি পাতা আছে, ই-পাসপোর্টে তা থাকবে না। সেখানে থাকবে পলিমারের তৈরি একটি কার্ড। এই কার্ডের মধ্যে থাকবে একটি চিপ। সেই চিপে পাসপোর্টের বাহকের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। একইসাথেই-পাসপোর্টের সব তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষিত থাকবে ‘পাবলিক কি ডিরেক্টরি’তে (পিকেডি)। আন্তর্জাতিক এই তথ্যভান্ডার পরিচালনা করে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও)। ইন্টারপোলসহ বিশ্বের সব বিমান ও স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এই তথ্যভান্ডারে ঢুকে তথ্য যাচাই করতে পারে।
তাই শুরুতেই এমআরপি ডাটাবেজে যেসব তথ্য আছে তা স্থানান্তরের মাধ্যমেই তৈরি হবে আমাদের ই-পাসপোর্ট। এতে ৩৮ ধরনের নিরাপত্তা ফিচার থাকবে। পাসপোর্টের মেয়াদ হবে বয়সভেদে ৫ ও ১০ বছর। শুরুতে জার্মানি থেকে ২০ লাখ পাসপোর্ট ছাপিয়ে আনা হলেও বাংলাদেশেই ছাপানো হবে আরো ২ কোটি ৮০ লাখ পাসপোর্ট। এ জন্য উত্তরায় একটি কারখানাও স্থাপন করা হবে।
পাসপোর্ট অধিদফতর সূত্র জানায়, ই-পাসপোর্ট চালু হওয়ার সাথে সাথে এমআরপি পাসপোর্ট বাতিল হয়ে যাবে না। তবে কারও পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাকে এমআরপির বদলে ই-পাসপোর্ট নিতে হবে। ই-পাসপোর্টের বাহক কোনো দেশের দূতাবাসে ভিসার জন্য আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আবেদনকারীর তথ্যের সাথে পিকেডিতে সংরক্ষিত তথ্য যাচাই করে নেবে এবং আবেদন গ্রহণ করে বইয়ের পাতায় ভিসা স্টিকার কিংবা বাতিল করে সিল দেবে। স্থল ও বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষও একই পদ্ধতিতে পিকেডিতে ঢুকে ই-পাসপোর্টের তথ্য যাচাই করবে। অন্যদিকে ই-পাসপোর্ট চালুর জন্য দেশের প্রতিটি বিমান ও স্থলবন্দরে চাহিদা মোতাবেক ই-গেট স্থাপন করে স্বয়ংক্রিয় সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হবে।প্রকল্পের আওতায় ৫০টি ই-গেট নির্মাণ করা হবে। ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই গেট স্থাপন করা হবে।সাত বছর মেয়াদী এ প্রকল্পে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশালে ই-পাসপোর্টের কাজ চলবে। যাদের হাতে ই-পাসপোর্ট থাকবে, তাদের এই গেট দিয়ে সীমান্ত পার হতে হবে। তবে যাদের হাতে এমআরপি পাসপোর্ট থাকবে, তাদের ইমিগ্রেশনের কাজ বিদ্যমান পদ্ধতিতে চলমান থাকবে।
গেট পাস থেকে ই-পাসপোর্ট
কোনো একটি দেশের নির্দিষ্ট ভূখন্ড থেকে অপর একটি দেশের বন্দরে যাওয়ার অনুমতি হচ্ছে পাসপোর্ট (পাস + পোর্ট)। এর প্রচলন শুরু হয় মধ্যযুগে।ব্রিটেনের রাজা পঞ্চম হেনরির সময়ে। ওই সময়ে শুরুতে ইউরোপের দেশগুলোর কোনো শহর বা নগরে প্রবেশ করতে চাইলে নগর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গেটপাস নিতে হতো বিদেশি পর্যটক বা পরিব্রাজকদের। ১৫৪০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গেটপাস আইন ১৪১৪ হয় এবং ট্রাভেল ডকুমেন্ট হিসেবে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। এরপর ১৭৯৪ সালে তারা সরকারি চাকুরেদের জন্য পাসপোর্ট ইস্যু করে।
বিশ্বকোষ অনুযায়ী, আনুমানিক ৪৫০ খ্রিস্টাব্দে হিব্রু বাইবেলের নেহেমিয়া ২ঃ৭-৯তে পাসপোর্টের অনুরূপ কাগজের নথির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর মধ্যযুগীয় ইসলামিক খেলাফতের সময়, শুল্ক প্রদানের রসিদ ছিল এক ধরনের পাসপোর্ট। যারা জাকাত (মুসলিমদের জন্য) ও জিজিয়া কর (জিম্মিদের জন্য) প্রদান করত, শুধু সেইসব মানুষ খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতে পারত। এভাবে শুল্ক প্রদানের রসিদ ভ্রমণকারীদের জন্য পাসপোর্টের অনুরূপ ছিল।
তবে আন্তর্জাতিকভাবে আধুনিক পাসপোর্টের ধারণা শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে। মূলত, দেশগুলো নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এর ওপর জোর দেয়। তখন প্যারিসে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (লিগ অব ন্যাশনস) বৈঠকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কাগজের তৈরি পাসপোর্ট এবং আনুষঙ্গিক অন্য নিয়মকানুন চালু করা হয়। ১৯৮০ সালের পর আসে এমআরপির ধারণা। বাংলাদেশে এর প্রচলন শুরু হয় ২০১০ সালে। অবশ্য এর দু’বছর আগেই ২০০৮ সাল থেকে কন্টাক্টলেস স্মার্টকার্ড প্রযুক্তির (বায়োমেট্রিক পদ্ধতিনির্ভর) ডিজিটাল পাসপোর্ট বা ই-পাসপোর্ট চালু হয়। ওই বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের ৬০টি দেশ এই পাসপোর্ট চালু করে। নিরাপত্তা চিহ্ন হিসেবে ই-পাসপোর্টে থাকে চোখের মণির ছবি ও আঙুলের ছাপ। আর এর পাতায় থাকা চিপসে সংরক্ষিত থাকে পাসপোর্টধারীর সব তথ্য।
ই-পাসপোর্ট যুগে বাংলাদেশ
২০১৬ সালের ২৪ এপ্রিল পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ উদ্বোধনের সময় ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই অংশ হিসেবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০) আধুনিক ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ই-পাসপোর্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এরপর শেখ হাসিনার জার্মানি সফরের সময় ২০১৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে জার্মানির সরকারি প্রতিষ্ঠান ভেরিডোস জেএমবিএইচের সাথে সমঝোতা স্মারক সই হয়।
সরকারের বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিফতর সূত্র মতে, গত ১৫ মে অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ই-পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী ৫ জুন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে ই-পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব। প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে সরকারিভাবে বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা দেবে জার্মানি।
গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত কারিগরি কমিটির মোট ছয়টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এসব সভার তিনটিতে বাংলাদেশে জার্মানির রাষ্ট্র্রদূত ও উপরাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনা বিভাগ থেকে ই-পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব দ্রুত একনেক সভায় উত্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে তাগিদ দেয়া হয়।
এদিকে ই-পাসপোর্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জার্মানির একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে জুন-জুলাইয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি জানিয়েছেন, সরকার আশা করছে ডিসেম্ব^রের মধ্যে ই-পাসপোর্ট চালু করা সম্ভব হবে। তবে সেটা পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যাবে জার্মানির প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি হওয়ার পর। কারণ, কাজটা তারাই করবে। তারা যদি বলে ডিসেম্ব^রের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে না, সে ক্ষেত্রে সময় এক-দুই মাস বেশি লেগে যেতে পারে।
এমআরপি থেকে ই-পাসপোর্ট
মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বা এমআরপি হচ্ছে এমন একটি পাসপোর্ট, যাতে আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্য জলছাপের মাধ্যমে ছবির নিচে লুকায়িত থাকে। একই সাথে এতে থাকে একটি ‘মেশিন রিডেবল জোন (গজত)’, যা পাসপোর্ট বহনকারীর ব্যক্তিগত তথ্যবিবরণী ধারণ করে। এমআরজেড লাইনে লুকায়িত তথ্য শুধু নির্দিষ্ট মেশিনের মাধ্যমে পড়া যায়।
অন্যদিকে ই-পাসপোর্ট নামে পরিচিত বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের মতোই। তবে এতে স্মার্টকার্ড প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এই কার্ডে একটি মাইক্রোপ্রসেসর চিপ এবং অ্যান্টেনা বসানো থাকে। এ পাসপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাসপোর্টের ডাটা পেজ এবং চিপে সংরক্ষিত থাকে। ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও) ডক ৯৩০৩-এ এই ডকুমেন্ট ও চিপ সংক্রান্ত তথ্য জমা রাখা হয়। তবে বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু আছে এমন দেশগুলো এ সংস্থার পাবলিক কি ডিরেক্টরির (পিকেডি) অংশ।
সুবিধা-অসুবিধার ই-পাসপোর্ট
ই-পাসপোর্টের আইডেন্টিফিকেশন ব্যবস্থায় বর্তমানে ফেসিয়াল, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং আইরিস রিকগনিশন বায়োমেট্রিকস ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে আইসিএও পাসপোর্টে ব্যবহার্য বায়োমেট্রিক ফাইল ফরম্যাট এবং যোগাযোগ প্রটোকল নির্ধারণ করে দেয়। ডিজিটাল ছবি চিপে শুধু ডিজিটাল ছবিই সংরক্ষিত রাখা হয়, যা সাধারণত জেপিইজি বা জেপিইজি২০০০ ফরম্যাটের হয়ে থাকে। পাসপোর্ট চিপের বাইরে ইলেকট্রনিক বর্ডার কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে এই বায়োমেট্রিক ফিচারগুলোর মধ্যে তুলনা করা হয়।
কন্টাক্টবিহীন চিপে ডাটা সুরক্ষিত রাখতে এতে কমপক্ষে ৩২ কিলোবাইট ‘ইইপিআরওএম, সংক্ষেপে ইইপিরম (ঊঊচজঙগ)’ স্টোরেজ মেমরি থাকে এবং তা আইএসও/আইআইইসি ১৪৪৪৩ আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডসহ আরও কিছু স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী একটি ইন্টারফেসে পরিচালিত হয়। তবে বিভিন্ন দেশ এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানভেদে এই স্ট্যান্ডার্ড ভিন্ন হয়ে থাকে। ইইপিরমের মানে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালি ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিড-অনলি মেমরি। এটি একটি বিশেষ ধরনের মেমরি, যা কমপিউটার এবং ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলোয় ব্যবহার করা হয়। এতে অপেক্ষাকৃত কম জায়গা থাকলেও এর প্রতিটি বাইট আলাদাভাবে মুছে ফেলা বা আবার প্রোগ্রাম করা যায়। এর ফলে পাসপোর্টের তথ্য আপডেট করতে কোনো সমস্যা হবে না।
ই-পাসপোর্টে ঝুঁকি
বায়োমেট্রিক পাসপোর্টে সাইবার আক্রমণ ঠেকাতে নন-ট্রেইসেবল চিপ ব্যবহারসহ আরও কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু থাকে। বিভিন্ন চিপ আইডেন্টিফায়ার প্রতিটি আবেদনের বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন চিপ নাম্বার দিয়ে থাকে। পাসপোর্ট চিপে রক্ষিত তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পিকেআই) ব্যবহার হয়, যার ফলে সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে চালু অবস্থায় এ ধরনের পাসপোর্ট নকল করা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়বহুল। একইসাথে ই-পাসপোর্টের ডাটা প্রাইভেসি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শুরু থেকেই। অনেক দেশেই এ নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অভিযোগ হচ্ছে, পাসপোর্টের ডাটা তারবিহীন আরএফআইডি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্রান্সফার করা যেতে পারে, আর এ কারণে ঘটতে পারে বড় ধরনের ডাটা হাতিয়ে নেয়ার ঘটনা। যদি পাসপোর্টের চিপে থাকা ব্যক্তিগত তথ্য আর পাসপোর্ট নাম্ব^ার সঠিকভাবে এনক্রিপ্ট করে না রাখা হয়, তাহলে এই তথ্য যেকোনো সময় অপরাধীদের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
ই-পাসপোর্টের ডাটা সুরক্ষা পদ্ধতি
সাধারণত বেসিক, প্যাসিভ, অ্যাকটিভ ও এক্সটেন্ডেড পদ্ধতিতে ই-পাসপোর্টের ডাটা সুরক্ষা করা হয়। আর তথ্য যাচাই করতে অটোমেটিক বর্ডার কন্ট্রোল সিস্টেমে (ই-গেট) ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষার বর্ণ নিয়ে গঠিত নামগুলোর ক্ষেত্রে পাসপোর্টের নন-রিডেবল জোনে লোকাল স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে উচ্চারণের জটিলতা দূর করে। তবে মেশিন-রিডেবল জোনের ক্ষেত্রে আইসিএওর স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ভিন্ন উচ্চারণভঙ্গির বর্ণগুলোকে সরল রূপ দেয়া হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি ম্যাপিং অনুসরণ করা হয়।
ক. বেসিক অ্যাকসেস কন্ট্রোল (বিএসি) পদ্ধতিতে চিপ এবং রিডারের মধ্যে যোগাযোগ সুরক্ষিত রাখতে এনক্রিপটেড তথ্য বিনিময় করা হয়। চিপের তথ্য পড়ার ক্ষেত্রে মেশিন রিডেবল জোন থেকে প্রাপ্ত একটি ‘কি’প্রবেশ করাতে হয়। মেশিন রিডেবল জোনে ব্যবহারকারীর জন্ম তারিখ, পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ এবং ডকুমেন্ট নাম্বার অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিএসি ব্যবহারের কারণে আক্রমণকারীরা যথাযথ ‘কি’ না জেনে তথ্যে আড়ি পাততে পারে না। তবে বিএসির কিছু দুর্বলতার কারণে বর্তমানে এর বিকল্প হিসেবে সাপ্লিমেন্টাল অ্যাক্সেস কন্ট্রোল (এসএসি) চালু রয়েছে।
খ. প্যাসিভ অথেনটিকেশন (পিএ) পদ্ধতিতে পাসপোর্ট চিপে রক্ষিত তথ্যে কোনো পরিবর্তন চিহ্নিত করতে ব্যবহার হয়। চিপে একটি এসওডি ফাইল থাকে, যাতে চিপে রক্ষিত সব তথ্যের হ্যাশ ভ্যালু এবং এদের একটি ডিজিটাল সিগনেচার উল্লিখিত থাকে। চিপের কোনো তথ্য পরিবর্তন করা হলেই হ্যাশ ভ্যালুর ভিন্নতা থেকে তা শনাক্ত করা হয়। বায়োমেট্রিক পাসপোর্টে পিএ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। এখানে একটি ডিজিটাল স্বাক্ষর রাখা হয়, এটি রাষ্ট্রের সাইনিং কি সংবলিত একটি ডকুমেন্ট সাইনিং কি ব্যবহার করে বানানো হয়।
গ. অ্যাকটিভ অথেনটিকেশন (এএ) পদ্ধতিতে ব্যবহার করে নকল পাসপোর্ট চিপ তৈরি ঠেকানো হয়। এতে একটি ব্যক্তিগত ‘কি’ থাকে, যা নকল করা সম্ভব না হলেও এর অস্তিত্ব সহজেই প্রমাণ করা যায়।
ঘ. এক্সটেন্ডেড অ্যাকসেস কন্ট্রোল (ইএসি)পদ্ধতিতে ব্যবহারে চিপ এবং রিডার উভয়েরই নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করা হয়। এই ব্যবস্থা সাধারণত ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং আইরিস স্ক্যান সুরক্ষিত রাখতে ব্যবহার হয় এবং এর এনক্রিপশন সিস্টেম বিএসির তুলনায় শক্তিশালী। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে সব রকম ডকুমেন্টের জন্যই ইএসি ব্যবহার বর্তমানে বাধ্যতামূলক।
এ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও কিছু দেশে চিপে অনধিকার প্রবেশ ঠেকাতে পাসপোর্ট কাভারের নিচে খুবই পাতলা ধাতব পাত ব্যবহার করা হয়।
আমাদের ই-পাসপোর্ট
বর্তমানে বই আকারে যে পাসপোর্ট আছে, ই-পাসপোর্টের একই ধরনের বই থাকবে। তবে বর্তমানে পাসপোর্টের বইয়ের শুরুতে ব্যক্তির তথ্য সংবলিত যে দুটি পাতা আছে, ই-পাসপোর্টে তা থাকবে না। সেখানে থাকবে পলিমারের তৈরি একটি কার্ড। এই কার্ডের মধ্যে থাকবে একটি চিপ। সেই চিপে পাসপোর্টের বাহকের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। একইসাথেই-পাসপোর্টের সব তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষিত থাকবে ‘পাবলিক কি ডিরেক্টরি’তে (পিকেডি)। আন্তর্জাতিক এই তথ্যভান্ডার পরিচালনা করে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও)। ইন্টারপোলসহ বিশ্বের সব বিমান ও স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এই তথ্যভান্ডারে ঢুকে তথ্য যাচাই করতে পারে।
তাই শুরুতেই এমআরপি ডাটাবেজে যেসব তথ্য আছে তা স্থানান্তরের মাধ্যমেই তৈরি হবে আমাদের ই-পাসপোর্ট। এতে ৩৮ ধরনের নিরাপত্তা ফিচার থাকবে। পাসপোর্টের মেয়াদ হবে বয়সভেদে ৫ ও ১০ বছর। শুরুতে জার্মানি থেকে ২০ লাখ পাসপোর্ট ছাপিয়ে আনা হলেও বাংলাদেশেই ছাপানো হবে আরো ২ কোটি ৮০ লাখ পাসপোর্ট। এ জন্য উত্তরায় একটি কারখানাও স্থাপন করা হবে।
পাসপোর্ট অধিদফতর সূত্র জানায়, ই-পাসপোর্ট চালু হওয়ার সাথে সাথে এমআরপি পাসপোর্ট বাতিল হয়ে যাবে না। তবে কারও পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাকে এমআরপির বদলে ই-পাসপোর্ট নিতে হবে। ই-পাসপোর্টের বাহক কোনো দেশের দূতাবাসে ভিসার জন্য আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আবেদনকারীর তথ্যের সাথে পিকেডিতে সংরক্ষিত তথ্য যাচাই করে নেবে এবং আবেদন গ্রহণ করে বইয়ের পাতায় ভিসা স্টিকার কিংবা বাতিল করে সিল দেবে। স্থল ও বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষও একই পদ্ধতিতে পিকেডিতে ঢুকে ই-পাসপোর্টের তথ্য যাচাই করবে। অন্যদিকে ই-পাসপোর্ট চালুর জন্য দেশের প্রতিটি বিমান ও স্থলবন্দরে চাহিদা মোতাবেক ই-গেট স্থাপন করে স্বয়ংক্রিয় সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হবে।প্রকল্পের আওতায় ৫০টি ই-গেট নির্মাণ করা হবে। ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই গেট স্থাপন করা হবে।সাত বছর মেয়াদী এ প্রকল্পে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশালে ই-পাসপোর্টের কাজ চলবে। যাদের হাতে ই-পাসপোর্ট থাকবে, তাদের এই গেট দিয়ে সীমান্ত পার হতে হবে। তবে যাদের হাতে এমআরপি পাসপোর্ট থাকবে, তাদের ইমিগ্রেশনের কাজ বিদ্যমান পদ্ধতিতে চলমান থাকবে।
পাঠকের মন্তব্য
অনুরূপ লেখা